
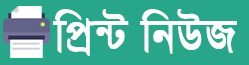
জাপান-বাংলাদেশের মধ্যাকার সম্পর্ক স্থাপনের যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তিনি হলেন বিচারক রাধা বিনোদ পাল। যার কারনে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছে জাপানের। যে সম্পর্কের জায়গা থেকেই জাপান বাংলাদেশকে দিয়ে যাচ্ছে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ঋণ ও সহায়তা।
সেই রাধা বিনোদ পালের জন্মস্থান কুষ্টিয়ার মিরপুরে গিয়ে তার জন্মস্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন।
ফেসবুকে তার পেজ থেকে লাইভে সরকারের কাছে এ আবেদন জানান তিনি।
রাধা বিনোদ পালের জন্মস্থানের বাড়ির সেখানে একটি পুকুরের সামনে দাড়িয়ে লাইভে তিনি বলেন – ‘জাপানের সাথে বাংলাদেশের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক, যে কারণে জাপান-বাংলাদেশকে অনেক বেশি পছন্দ করে এর একটি কারণ হলো বাংলাদেশের একজন মানুষ যিনি জাস্টিস রাধাবিনোদ পাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে মানুষটি জাপানিদের বিচার হচ্ছিল সেখানে তিনি সব জাপানীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলায় রাধাবিনোদ পালের জন্মস্থান এবং তিনি এখানে থাকতেন এবং তার স্মৃতি শুধু এই পুকুরটাযই আছে।’
তিনি পুকুরের মধ্যে পাওয়া কয়েকটা ইট দেখিয়ে বলেন – এখানে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে R.B.P মানে হচ্ছে গিয়ে রাধাবিনোদ পাল। যেহেতু আগের যুগে ইট ভাটা ছিলো না বরং সবাই নিজ উদ্যোগে ইট বানাতো তাই যে বানাতো সে যা ইচ্ছে লিখে নিতে পারতো ইটে। সে হিসেবেই তার নামের প্রথম অক্ষরগুলো এখানে রয়ে গেছে।
ব্যারিস্টার সুমন আফসোস নিয়ে বলেন – ‘এই মানুষটার স্মৃতি এখন পর্যন্ত কিছুই এখানে সংরক্ষণ করা হয় নাই। পেছনে যে বাড়িটা আছে ওই বাড়িটা একদম নিঝুম হয়ে গেছে। এখন এখানে কিছু নাই। তার জায়গার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা দখল হয়ে গেছে। আমার কথা হচ্ছে, যে মানুষটাকে সারা পৃথিবী রিকগনাইজ করল। যে মানুষটা বাংলাদেশকে বা বাঙালি জাতিকে এত সামনের দিকে নিয়ে গেল এই মানুষটার স্মৃতি সংরক্ষণ করেও আমরা দেখতে পারেনি। অথচ জাপানে তার স্মৃতিতে অনেক কিছু রয়েছে।’
ব্যারিস্টার সুমন বলেন – ‘আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব এই সম্মানী মানুষটির স্মৃতি সংরক্ষনের জন্য। কারন সম্মানী মানুষকে সম্মান না দিলে পরবর্তীতে আবার সম্মানী মানুষ জন্মাবে না।’
প্রসঙ্গত : রাধা বিনোদ পাল একজন বাঙালি আইনবিদ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দূরপ্রাচ্যে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের বিচারার্থে স্থাপিত আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। “জাপান-বন্ধু ভারতীয়” বলে খ্যাতি রয়েছে তার। জাপানের ইতিহাসে রাধা বিনোদের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। জাপানের টোকিও শহরে তার নামে জাদুঘর, সড়ক ও স্ট্যাচু রয়েছে। জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি রিসার্চ সেন্টার রয়েছে তার নামে। তিনি আইন সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের রচয়িতা।
[জাপানের জাসুকুনি মন্দিরে রাধাবিনোদ পাল স্মৃতিস্তম্ভ। স্মৃতিস্তম্ভে তার পরিচয় লেখা আছে ‘রাধাবিনোদ পাল, মিত্রবাহিনীর ১১ বিচারপতির মধ্যে একমাত্র বিচারক, যিনি টোকিও ট্রায়ালে জাপানের যুদ্ধকালীন শীর্ষ নেতাদের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।’]
রাধা বিনোদ পালের জন্ম ও পড়াশোনা :
১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কুষ্টিয়া জেলার তৎকালীন দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের মৌজা সালিমপুরের অধীন তারাগুনিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তার জন্ম। এলাকাটি এখন জজপাড়া নামে পরিচিত। তার পিতার নাম বিপিন বিহারি পাল।
তার প্রাথমিক জীবন চরম দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ছাতিয়ান ইউনিয়নের ছাতিয়ান গ্রামের গোলাম রহমান পণ্ডিতের কাছে তার শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি। তিনি তৎকালীন নদিয়া জেলার (বর্তমান কুষ্টিয়া) তারাগুনিয়া এল.পি স্কুলে (বর্তমানে তারাগুনিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ও পরে কুষ্টিয়া হাইস্কুলে তিনি মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করেন।
১৯০৫ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। পড়তেন গণিতশাস্ত্র নিয়ে। ১৯০৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গণিতে স্নাতকোত্তর পাস করেন। এরপর কিছুদিন এলাহাবাদে গিয়ে অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে কেরানীর চাকরি করেছিলেন। বিএল ডিগ্রী পাওয়ার পর চাকরি নিলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। গণিতের শিক্ষকতা করার পাশাপাশি ময়মনসিংহ কোর্টে ওকালতির চর্চাও চলছিল সমান তালে।
১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে এলএলএম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। এবার পালা উচ্চস্তরের আইন চর্চার। শিক্ষকতা ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে সেখানকার হাইকোর্টে আইনব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। আইনচর্চার তুলনায় রাধাবিনোদ পালকে বোধহয় বেশি টানত বিশ্লেষণ। তিনি চেয়েছিলেন আইন বিশারদ হতে। আইন তার কাছে শুধু পেশা ছিল না। তাহলে হাইকোর্টে আইন চর্চার সুযোগ পেয়েই থেমে যেতেন। ১৯২৪ সালে আইনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করলেন তিনি। যারা বলছিল, আইন চর্চার সুযোগ পেয়ে শিক্ষকতার মহান ব্রতকে ছেড়ে গেলেন রাধাবিনোদ, তাদের মুখে ছাই দিয়ে ইউনিভার্সিটি অব ল কলেজে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত আইনের অধ্যাপনা করেছিলেন তিনি।
জাপানের সাথে সম্পর্কের সূত্র :
রাধাবিনোদ পাল আন্তর্জাতিক আইন সংস্থাগুলোর সদস্যপদ লাভ করেন। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক দিক নয়, তার ন্যায় বিচারের সুখ্যাতিও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তখনও ভারতে ইংরেজ শাসন চলছে। তার মাঝেই ১৯৪১ সালে তিনি ভারত সরকারের আইন উপদেষ্টা, তারপর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এরপর ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। তখন ১৯৪৬ সাল, কাজের চাপ কি নুইয়ে ফেলেছিল রাধাবিনোদ পালকে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ফিরে এলেন বাংলাদেশে, শেকড়ের তরে। সলিমপুরের মাটির ঘ্রাণেই বাকিটা জীবন শান্তিতে কাটাতে চান। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনা ছিল অন্যরকম।
দূরপ্রাচ্য বিষয়ক আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনাল তাকে বিচারক হিসেবে চাইছে। সেখানে ১১ জনের একজন হয়ে যাবেন তিনি। আন্তর্জাতিক অপরাধের ‘ন্যায়বিচার’ করবেন। কিন্তু টোকিও পৌঁছে তার ভুল ভাঙল। তাকে মেধাবী যোগ্য বিচারক হিসেবে এখানে আনা হয়নি। বরং অবহেলিত দেশের ক্ষুদ্র প্রতিনিধি হিসেবে বিচারকদের প্যানেলে একটা সমতা রক্ষার জন্য আনা হয়েছে। সেখানে রাধাবিনোদ কী মতামত দেন তা কারোর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল আলাদা একটি হোটেলে। বাকি ১০ জনের জন্য ছিল ভিন্ন ব্যবস্থা।
বিচারের সময় চলে এলে রাধাবিনোদ ভিন্নমত পোষণ করলেন। জাপান যুদ্ধের আগে ও যুদ্ধচলাকালে যে কম অপরাধ ঘটায়নি তা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু দোষ শুধু জাপানের একার ছিল না। নাগাসাকি, হিরোশিমাতে বোমাবাজি করে মানবতার অপমান না করলেও জাপান আত্মসমর্পণ করতো। এইসব যুদ্ধাপরাধের জন্য, হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যার জন্য এই শক্তিশালী দেশগুলোরও তাহলে শাস্তি পাওনা আছে। তার এই কথায় ফুঁসে উঠল প্যানেল। তাদের ধারণা, ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্যের আগ্রাসন বিরোধী এই বাঙালি নিতান্তই মিত্রশক্তি বিদ্বেষী।
অভিযোগগুলোর তিনটি ভাগ ছিল- এ, বি ও সি। এ শ্রেণীর অভিযোগ ছিল শান্তিবিরোধী অপরাধ। বি আর সি শ্রেণীতে ছিল প্রচলিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ। রাধাবিনোদ পাল ট্রাইব্যুনালকে মনে করিয়ে দিলেন এ এবং সি শ্রেণীর অভিযোগ কার্যকর হবে না। কারণ জাপান যখন যুদ্ধে যায় তখনও আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোনো আইন অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যদি আইনই না থাকে, তাহলে জাপান আইন কিভাবে ভাঙল? পুরো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিয়ে রাধাবিনোদ লিখলেন তার ঐতিহাসিক রায়। যার কিয়দংশ প্রকাশিত হয়েছে।
ধারণা করা হয়, এই রায় ছিল ১,২৩৫ পৃষ্ঠার। তিনি লিখেছিলেন জাপান তার অধিকৃত ভূমিতে যা করেছে তা ন্যাক্কারজনক, কিন্তু যে লোকগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি ট্রাইব্যুনাল। তিনি তার রায়ে প্রশ্ন রেখেছিলেন, অভিযুক্তদের করা অপরাধ যুক্তরাষ্ট্রের হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে করা অপরাধের চেয়েও বেশি ঘৃণ্য কিনা। যুদ্ধচলাকালে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিমানবাহিনী শত্রুদেশের সাধারণ নাগরিকদের সর্বোচ্চ মৃত্যু নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিল।
রাধাবিনোদ জাপানের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ভাববার অবসর নেই জাপান যা করেছিল, তিনি তার পক্ষে ছিলেন। বর্তমান সময়ে, জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিজের আগ্রাসী ভূমিকা লুকাতে রাধাবিনোদ পালের রায়কে ব্যবহার করে। তিনি বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এই ঘটনায় খুশি হতেন না। ১৯৫২ সালে হিরোশিমায় এক বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি বলেন, “জাপান যদি আবারো সমরবাদের উত্থান চায়, তবে তা হবে, এইখানে, এই হিরোশিমায় শায়িত নিরীহ মানুষদের আত্মার প্রতি চরম অসম্মান।”
তার রায় এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ফরাসী আর ডাচ বিচারকেরা তা থেকে প্রভাবিত হয়ে কিছুটা নিরপেক্ষ অবস্থানে সরে আসেন। তবে মিত্রশক্তির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তারা নিজেদের রায়ে জাপানি অফিসারদের শাস্তি চাইতে ভোলেননি। রাধাবিনোদ পালের মূল রায়টির কিছু অংশ অনেক বছর পর জাপান সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এই শর্তে যে, তারা ট্রাইব্যুনালের রায় মেনে নেবে।
বিচারকার্য শেষ হতে হতে ১৯৪৮ সাল চলে এল। ভারত তখন আর কারো উপনিবেশ নয়। রাধাবিনোদ পালও তখন ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্ত একজন মানুষ। ট্রাইব্যুনালের আশা ছিল দরিদ্র উপনিবেশের বাসিন্দা হয়তো কোনোরকম উচ্চবাচ্চ্য ছাড়াই বাকিদের রায়ের অনুরূপ রায় দেবে। কিন্তু তার রায় দেখে মুখ বাঁকিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, “ওসব নিরপেক্ষতা একজন পরাধীন মানুষের শক্তিশালী দেশের সাথে ঈর্ষা ছাড়া কিছু নয়”।
তিনি জাপান-বন্ধু ভারতীয় বলে খ্যাতি অর্জন করেন। রাধাবিনোদ পালকে সম্মানসূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করা হয় নিহোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ১৯৬৬ সালে। জাপান সম্রাট হিরোহিতোর কাছ থেকে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মানীয় পদক ‘কোক্কা কুনশোও’ গ্রহণ করেছিলেন। জাপানের রাজধানী টোকিও তে তার নামে রাস্তা রয়েছে। কিয়োটো শহরে তার নামে রয়েছে জাদুঘর, রাস্তার নামকরণ ও স্ট্যাচু। টোকিও ট্রায়াল টেলিসিরিয়ালটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধাপরাধীদের ট্রায়াল নিয়ে নির্মিত হলে তার চরিত্রে অভিনয় করেন ভারতীয় অভিনেতা ইরফান খান।
শেষ জীবন :
স্বাধীন দেশে ফিরে এলেন রাধাবিনোদ। তার দেশেও তখন চলছে স্বাধীনতা উত্তর অরাজকতা। তার অবসর নেওয়া আর হয়ে উঠল না। ১৯৫৮ সালে জাতিসংঘের আইন কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। জাপানেও গিয়েছেন বেশ কয়েকবার। ১৯৬৬ সালে জাপানের সম্রাট তাকে জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্মান ‘প্রথম শ্রেণীর পবিত্র রত্ন’তে ভূষিত করলেন।
তিনি ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তার সম্মানে ইয়াসুকুনি মঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।
ইতিকথা :
প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব রাধা বিনোদ পালের সুখ্যাতি শুধু পাকিস্তান-ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৬-৪৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও মহানগরে জাপানকে নানচিং গণহত্যা সহ দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধে চীনাদের উপর জাপানি সেনাবাহিনীর দীর্ঘ কয়েক দশকের নৃশংসতার অভিযোগে যুদ্ধাপরাধী সাব্যস্ত করে যে বিশেষ আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার হয়, তিনি ছিলেন সেই আদালতের অন্যতম বিচারপতি। তিনি তার ৮০০ পৃষ্ঠার বিচক্ষণ রায় দিয়ে জাপানকে “যুদ্ধাপরাধ”-এর অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন। এ রায় বিশ্বনন্দিত ঐতিহাসিক রায়ের মর্যাদা লাভ করে। তার এ রায় জাপানকে সহিংসতার দীর্ঘ পরম্পরা ত্যাগ করে সভ্য ও উন্নত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশে প্রধানতম সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।
এই মহান বীর, যিনি অকুতোভয় কন্ঠে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একা লড়ে গেছেন, তিনি নিজ জাতির কাছে পর্যাপ্ত সম্মানটুকু পাননি। কুষ্টিয়ায় তার ভিটেবাড়ি এখন অরক্ষিত। তার নাম উল্লেখ করা হয়নি কোনো পাঠ্যবইয়ে। যে ব্যক্তি শক্তিশালী দেশের সাথে সুসম্পর্কের প্রলোভন ভুলে নিজের মতো চলেছেন দিব্যি, আমাদের স্মৃতিতে তাকে ধরে রেখেছি কিনা এতটুকু নিয়ে অভিমান করার মতো তিনি নন নিশ্চয়ই। কিন্তু একজন বাঙালি হিসেবে, একজন বাংলাদেশি হিসেবে আপনি আমি তার মত মানুষগুলোকে মনে রাখার ছোট্ট দায়িত্বটার কতটুকু পালন করেছি তো!?
তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া, রোর বাংলা। সম্পাদনা : হাছিব আর রহমান।



