
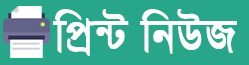
লেখাটির পূর্ব শিরোনাম ছিলো ‘ঢাবির অধীনে ঢাকার ৭ কলেজ; কিছু কথা কিছু ব্যাথা’। লেখাটি তৈরি করা হয়েছিলো প্রায় দেড় বছর আগে; গত বছর মার্চে। লেখাটি তখন কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। লিখেছিলাম মনের আবেগ-ক্ষোভ থেকে। কিন্তু প্রকাশ করা হয়নি কেন? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছিলাম কী লাভ হবে! কোনো লাভ নেই, কেউ শুনবে না ভুক্তভোগীদের কথা। ভোগান্তিতে পড়ার আগেই শুনেনি কেউ; তখনো শুনবে বলে মনে হয়নি। এজন্য পরে আর লেখাটি প্রকাশ হয়ে ওঠেনি। কেউ হয়তো বলতে পারেন এতোদিন পরে এসে কেন প্রকাশ করলাম। এর উত্তর হলো নিরাশার মাঝেও আমরা বাঙালিরা আশান্বিত হতে ভালোবাসি।
সম্প্রতি সাত কলেজ নিয়ে দ্বিমুখী আন্দোলন শুরু হয়েছে। সংকটের আকার বেড়ে গভীর খাঁদ সৃষ্টি হয়েছে। তাই মনে হলো অন্তত যেটুকু ক্ষতি হয়েছে তার থেকে আরো ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় সেই দাবিতে নিজেও একজন ভুক্তভোগী হিসেবে কথাগুলো বলা দরকার; যদি কেউ শুনেন এই আশায়। লেখাটি পূর্বের সময়কালীন ভাবনাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। কিছু জায়গায় যেটুকু আপডেট/পরিবর্তন হয়েছে তা সংযুক্ত করে পূর্বের লেখাটি হুবহু প্রকাশ করা হলো:-
অনেক জল্পনা-কল্পনা শেষে ঢাকার ৭ সরকারী কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত করা হয়েছে প্রায় ১ বছর হলো (বর্তমানে প্রায় আড়াই বছর হতে চলছে)। যদিও এর শেষ কোথায়, ফলাফল কী তাও অদৌও এখনো অজানা সংশ্লিষ্ট মহলে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মাঝে এখনো রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। মিশ্র প্রতিক্রিয়ার কারণ হলো শিক্ষার্থীরা এখনো বুঝে উঠতে পারেনি ঢাবির অধিভুক্ত হওয়ায় তাদের আসলে কতটুকু উপকার হয়েছে। অনেকের কাছে বিষয়টি না চাইতেই চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো হলেও কিছু শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়টা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাদের কাছে এই সিদ্ধান্তটা আত্মসম্মানহানী ও হারানোর বেদনায় হতাশ হওয়ার মতোও।
কারণ এরা ব্যতিক্রম, এরা অন্যের চেয়ে কিছুটা আলাদা। এরা গভীরভাবে ভাবতে জানে। এরা কল্যাণ-অকল্যাণ খুঁজে বের করতে জানে। তারা জানে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে কুঁড়ির মুকুলে থাকা তাদের একটি স্বপ্ন পাপড়ি হয়ে ফোটার আগেই ঝড়ে গেছে। স্বপ্নটার কথা পরে জানবো আমরা। তার আগে জেনে নেই কীভাবে এই সিদ্ধান্তটা বাস্তবায়ন হলো।
এক.
অলোচিত সাত কলেজকে ঢাবির অধিভুক্ত করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। প্রধানমন্ত্রী কেন এই নির্দেশ দিয়েছেন! নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীদের কল্যাণ হবে এটা বিবেচনা করেই। আর সেটা করেছেন শিক্ষাবিদদের পরামর্শ নিয়েই। হয়তো কোনো শিক্ষাবিদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এভাবেই বুঝিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ ছিলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি কলেজগুলো অঞ্চলভেদে সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছেড়ে দেয়ার।
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হওয়ায় শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদেরও কেউই প্রকাশ্যে এর নেতিবাচক দিক সম্পর্কে কিছু বলার সাহস করেননি। তবে ‘অব দ্য রেকর্ড’ সরকার বিরোধী নয় বরং সরকারপন্থী বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদেরও বেশির ভাগই এ ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়নের আগে ভেবে দেখার তাগিদ দিয়েছিলেন। তাদের মতে, ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কলেজ পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ার কারণেই ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলো পরিচালনার ভার দেয়া হয়। তাই কলেজগুলো আগের জায়গায় পাঠালে দেশ আবার ২৪ বছর পূর্বে ফিরে যাবে। তাছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিজেরাই নানান সমস্যায় জর্জরিত’।
২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে উল্লিখিত নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্র মতে, ‘প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একাধিক বৈঠক করে ইউজিসি। এরমধ্যে প্রথম বৈঠকে ভিসিদের পক্ষ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসে। বেশির ভাগ ভিসি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের পক্ষে মত দিলেও তারা একটা ‘তবে’ রেখে মতামত দেন। ওই তবে হচ্ছে, বাড়তি কলেজ দিতে হলে অবকাঠামো, জনবল এবং নতুন বরাদ্দ দিতে হবে। বিপরীত দিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজস্ব খাতে বর্তমানে সরকার কোনো বরাদ্দ দেয় না। দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজের আয়ে চলে থাকে’।
জানা গেছে, এরপর এ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে একাধিক কমিটি গঠন করেছিলো ইউজিসি। কমিটিগুলো সুপারিশ তৈরির মধ্যেই কাজ সীমিত রাখে। এমতঅবস্থায় ২ বছর ৩ মাস পার হয়ে যায়। অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি জানতে চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বারবার তাগিদ আসে। এমন পরিস্থিতি ইউজিসির দ্বিতীয় কমিটি দেশের ১৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ করে ২৭৬টি কলেজ ভাগ করে দেয়। ভাগ-বাটোয়ারা অনুযায়ী ঢাকা কলেজ, তিতুমীর কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ইডেন ও বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ এবং আনন্দমোহন কলেজসহ ৩৩টি কলেজ ঢাবিভুক্ত হয়। এভাবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় সর্বনিম্ন ১ টি থেকে সর্বোচ্চ ২০টি কলেজ পায়।
ইউজিসি, কমিটির পাশাপাশি বিভিন্ন ভার্সিটির কাছে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কী কী লাগবে সে তথ্য চায়। এ ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য দিতে গড়িমসি করে। কয়েক দফা তাগিদের পর পূর্ণাঙ্গ তথ্য পায় ইউজিসি। সে হিসেবে অবকাঠামো, বাজেট, জনবলসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার দাবি আসে। ইউজিসির একজন কর্মকর্তা জানান, এ হিসাব তৈরির পর আরো ২৬৩টি কলেজ সরকারি হয়েছে। যদি এসব কলেজও উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে ছেড়ে দিতে হয়, তাহলে খরচ আরো বাড়বে। (যুগান্তর ০৪ এপ্রিল ১৭)।
দুই.
এই সামান্য পর্যালোচনায় কিছুটা হলেও আন্দাজ করা যায় কলেজগুলো ঢাবির অধীভুক্ত করা কতোটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যর্থতার কারণেই ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দীর্ঘ ২৪ বছর পরে একটা প্রতিষ্ঠান যখন ব্যর্থতা কাটিয়ে সবেমাত্র সফলতার আলোর মুখ দেখা শুরু করেছে সেই মুহর্তে সফল প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে পুরনো সেই ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে দেয়া শতভাগ অযৌক্তিক না হলেও যৌক্তিক যে হয়নি সেটা সচেতন মহলের কাছে সুস্পষ্ট।
মাননীয় প্রধানন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটা বিশেষ মহলের পক্ষ থেকে যেভাবে বুঝানো হয়েছে সিদ্ধান্তটা ঠিক সেভাবেই হয়েছে এটা সুস্পষ্ট। এই কাজটা কেন করা হয়েছে যারা করেছেন তারাই বলতে পারবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও একজন মানুষ। তার হাজারো দায়িত্ব আছে। তার একার পক্ষে সম্ভব নয় কোনো মাধ্যম ছাড়া সব বিষয়ে সার্বিক খোঁজ খবর নিয়ে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া। বরং যারা দয়িত্বপ্রাপ্ত হন তাদের পরামর্শ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কাজ করবেন এটাই স্বাভাবিক। এখন পরামর্শ দাতা কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যদি ব্যক্তি স্বার্থের কারণে কোনো ভুল পরামর্শ দিয়ে থাকেন তার দায়ভার তাদেরকেই নিতে হবে। কিন্তু দূর্ভাগ্য এই দায়ভারটা যারা ভোগান্তির স্বীকার হন তাদেরকেই নিতে হচ্ছে। অন্যদিকে সমালোচনা যা হওয়ার সেটা হচ্ছে সরকারের।
তিন.
বাঙালি অল্পতেই তুষ্ট বলতে আমাদের একটা প্রশংসনীয় গুণ আছে। তেমনিভাবে পরিশ্রম করে কোনো কিছু অর্জন করার চেষ্টা না করা, সুযোগ পেলে অন্যের গুণ ও যোগ্যতা ধার করে গর্ব করার একটা বদ গুণও আমাদের আছে। আর এই সুযোগটা পেলে পরিশ্রম করে যে নিজে একটা যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে; বাঙালি সেটাও ভুলে যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলাদেশে যতগুলো সরকারি বেসরকারি কলেজে অনার্স পাঠ দান করা হয় প্রত্যেকটি কলেজেরই একটা স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই! অনার্সের শিক্ষার্থীরা স্ব স্ব কলেজের পরিচয় না দিয়ে নিজেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষার্থী হিসেবেই পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে। বিশেষ করে বেসরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে। বলা যায় তারা এই উৎসাহটা পায় মূলত কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেইে।
বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে দেয়া শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য সুত্র মতে, বাংলাদেশের শিক্ষা আইনে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ নামে কোনো কলেজ নাই। কিন্তু বাস্তবে অনার্স পাঠদানের অনুমোদন প্রাপ্ত যতগুলো বেসরকারি কলেজ আছে নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে সবগুলো কলেজের নামের আগে বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত করা হয়েছে। ফলে অন্যের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত করার এই ভুল শিক্ষাটা শিক্ষার্থীরা আপন শিক্ষালয় থেকেই গ্রহণ করছে। সারাদেশের বেসরকারি কলেজগুলো বিশেষ করে ঢাকা শহরের শিক্ষার্থীরা নিজের পরিচয় এমনভাবে উপস্থাপন করে মনে হয় যেন তারা সরাসরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করছে।
যেই ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি জাতীয় বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী না হয়েও নিজেকে জাতীয় বিশ্বাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে সেসব শিক্ষার্থীর জন্য প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দিতে পারাটা না চাইতে চাঁদ পাওয়ার মতোই।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীভুক্ত কলেজগুলো এক একটা স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার স্বপ্ন দেখে। বিশেষ করে যে সব সরকারি কলেজ জনবল ও অবকাঠমোগত দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ সেসব কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করার একটা যৌক্তিক দাবিও উঠেছে বিভিন্ন কলেজে । ঢাকার যে সাত কলেজকে ঢাবিভুক্ত করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে একাধিক কলেজ জনবল, অবকাঠামো ও অবস্থানগত কারণে বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার যোগ্যতা ও যৌক্তিক দাবি রাখে। অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষ ও সচেতন শিক্ষার্থীদের এই স্বপ্নটা কলি হয়ে ফোটার আগেই ধ্বংস করে দেয়া হলো পরিকল্পিকভাবে, সুকৌশলে।
কলেজের লাস্ট বেঞ্চের শিক্ষার্থীরা এখন নিজেদের স্বাতন্ত্রতা ভুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় দিয়ে নিজেকে জাতে ওঠানোর চেষ্টা করছে। অন্য দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ ছাপিয়ে সাফ জানিয়ে দিয়েছে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাবির পরিচয় দিতে পারবে না। এ নিয়ে ঢাবি ও সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে সংঘর্ষ এবং ঢাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের খবরও গণমাধ্যমে এসেছে। বিষয়টা এখন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কাছে হাস্যকর এবং লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
চার.
সাত কলেজেকে ঢাবি অধীভুক্ত করার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে পুলিশি হামলায় এক শিক্ষার্থীর স্রষ্টার দেয়া অন্যতম শ্রেষ্ট নেয়ামত দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে। সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপে ওই শিক্ষার্থী একটা চাকরি পেলেও অপূর্ব সুন্দর পৃথিবী দেখার যে শক্তি হারিয়েছে সেট আর কখনো ফিরে আসবে না। চোখের আলোয় সে আর কখনো দেখতে পারবে না নয়ানাভিরাম এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য! দেখতে পারবে না তার আপনজনদেরকে। কিন্তু কেন পারবে না, কে নেবে এর দায়ভার? কে দেবে এর জবাব?
২০১৬-১৭ সেশনে কলেজগুলোকে ঢাবিভুক্ত করার পর প্রথম বর্ষের পরীক্ষা নেয়া হলো ২০১৮ সনে এসে। অন্যদিকে ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থীরা যথা সময়ে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছিলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তাদেরকেও নেয়া হয়েছে ঢাবির অধীনে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাদের দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিলো ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। একই ব্যাচের অন্যান্য কলেজগুলোর পরীক্ষা যথা সময়ে নিয়েও ফেলেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ ২০১৮ সালে এসেও এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা দিতে পারেনি সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাদের জীবন থেকে একটা বছরের অর্ধেক ইতোমধ্যেই অতীত হয়ে গেছে অনিশ্চয়তা ও অবহেলায়। পরীক্ষা কবে তাও এখনো অনিশ্চিত। আছে কি গত হওয়া এই এক বছর ফিরিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ? শঙ্কা হচ্ছে জুনিয়র ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এখন তাদের সিনিয়র হয়ে যাবে তারা থাকবে পেছনে পড়ে। এই অসম প্রতিযোগিতার দায়ভার কে নেবে আছে কি এর কোনো উত্তর?
সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকার সরকারি ৭ কলেজ সহ মোট ৩৩টি কলেজ ঢাবির অধীনে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি আরো ২৪৩ টি কলেজ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনের নেয়া হয়েছে। যেটা হয়েছে সেটা না হয় মেনে নেয়া হলো কিন্তু ২০১৬-১৭ সেশনের শিক্ষার্থীদের থেকেই যদি এই অধিভুক্তি কার্যকর করা হতো তাহলে অন্তত ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের এই ভোগান্তির স্বীকার হতে হতো না। তিন শিক্ষা বর্ষের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা একটা বোর্ড তথা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হয়ে গেছে সেই শিক্ষার্থীদের কোন যুক্তিতে শিক্ষাবর্ষ শেষ না করে অন্য আরেকটি বোর্ডের অধীনে নেয়া হলো? এদের বাকী পরীক্ষাগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করলে ঢাবির কী এমন ক্ষতি হতো? কার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীদের ভাগ্য নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলা হলো? কেন তাদের শিক্ষা জীবনের এই মূল্যবান সময়টা নষ্ট করা হলো? এখন দ্বিতীয় বর্ষ থেকে বাকী পরীক্ষাগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নিলো কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থীদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষার সনদ না দেয় তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে কী করবে? কী পদক্ষেপ নিবে ঢাবি কর্তৃপক্ষ? ব্যক্তিগত পর্যায়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মহল থেকে এমন কথাও শোনা গেছে। এটাই যদি বাস্তব হয় তাহলে ঢাবি কর্তৃপক্ষ কী করবে এসব শিক্ষার্থীদের জন্য?
নতুন বছরে নতুন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সচেতন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আকুল আবেদন এই অনিশ্চয়তার দোলাচল থেকে শিক্ষার্থীদের উদ্ধার করুন। জনবল, অবস্থান, অবকাঠামো ও শিক্ষার মান বিবেচনায় যৌক্তিক দাবি সম্পন্ন কলেজকে স্বায়ত্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দিন। বর্তমান এই সংকট মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশ দিন। ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষার্থীরা শেষ ভরসা হিসেবে আপনার দিকেই তাকিয়ে আছে।
পাঁচ.
লেখাটা এখানেই সমাপ্তি টানা হয়েছিলো। কিছু আবেগ, কিছু অভিমান, কিছু ভোগান্তি জনিত চাপা কষ্টের কথা লিখেছিলাম। আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে একজন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী। নিজের ইচ্ছাতেই একবছর পিছিয়ে (বিষয় পছন্দ পরিবর্তিত কারণে) ২০১৫-১৬ সেশনে সমাজ বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছিলাম তিতুমীর কলেজে। একাডেমিক ইয়ার অনুযায়ী এবছর আমার চুতর্থ বর্ষ অর্থাৎ অনার্স শেষ করার কথা ছিলো। কিন্তু সবেমাত্র তৃতীয় বর্ষের ফরম ফিলাপ চলছে। রুটিনের জন্য অপেক্ষ করতে হবে আরো কয়েকদিন। অধিভুক্তির প্রায় আড়াই বছর পার হওয়ার পর এই যখন পরিস্থিতি ঠিক তখন নতুন করে শুরু হয়েছে অধিভুক্তি বাতিলের আন্দোলন। আন্দোলন চলছে। দুই গ্রুপে। সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা চাচ্ছে এখন আর অধিভুক্তি বাতিল না করে বিদম্যান যাবতীয় সমস্যা নিরসন করার কথা। অন্যদিকে ঢাবি শিক্ষার্থীরা বলছে অধিভুক্তি বাতিল করা হোক।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ডাকসুর এজিএস সাদ্দাম হোসেন, সাত কলেজ অধিভুক্তিকে ‘আনহ্যাপি ম্যারিজ’ উপমা দিয়ে ‘পিসফুল ডির্ভোস’ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন। সেই সাথে বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদেরকে আগামী আগস্টের মধ্যে এর সমাধানের আশ্বাস দিয়ে দায়িত্ব নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ডাকবুর জিএস গোলাম রাব্বানী। এদিকে আন্দোলনের দুই মেরুতে অবস্থান করলেও ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আকতার হোসেন, একটি বেসরকারি টেলিভিশনে দেয়া সংলাপে বলেছেন, ঢাবি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন তারা সাত কলেজ সামাল দিতে পারছেন না। যদিও কর্তৃপক্ষ কখনোই এমনটা বলেও থাকলেও প্রকাশ্যে স্বীকার করবেন না।
ঢাবি শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনে ছাত্রলীগের সমর্থনের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবয়াদুল কাদের বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদেশে আছেন। তিনি দেশে ফিরলে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধান দিবেন। এর মানে হলো খুব সম্ভবত অধিভুক্তি বাতিলের দাবিটা গুরুত্ব পাবে আলোচনার টেবিলে। কিন্তু এই মুহুর্তে সত্যি সত্যি এমন সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এর পরিণাম যে কী হবে তা অনুমান করা না গেলেও সুখকর যে হবে না; তা অন্তত হলফ করে বলা যাবে।
তো যাই হোক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসার পর সিদ্ধান্ত হবে। নতুন করে ভাগ্য নির্ধারণ হবে সাত কলেজের। এই এক ‘অধিভুক্তি’ এখন একদিকে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের গলার কাঁটা। অন্যদিকে ‘অধিভুক্ত’ সাত কলেজ ঢাবি কর্তৃপক্ষের গলার কাঁটায় পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট শিক্ষার্থীদের আকুল আবেদন থাকবে এই গলার কাঁটা যেন রয়ে-সয়ে নামানো হয়। যেন এটা আবার কোনো নতুন ভাগ্যের খেলায় মরণ ফাঁদ হয়ে না ওঠে। উপযুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে যৌক্তিক পরিবেশ সৃষ্টি করে অথিভুক্তি বাতিল কিংবা বিদ্যমান সমস্যা নিরসনের যেই সিদ্ধানই আসুক শিক্ষার্থীরা মেনে নিবে। কিন্তু তার গ্যারান্টি কে দিবে সেটাই হলো বড় ভয়। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দুই দিকেই যৌক্তিক পরমর্শ হয়তো আছে কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে না। অধিভুক্ত করাটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিলো কিনা সেই প্রশ্ন এখনো আছে। কিন্তু এখন যদি বাতিল করা হয় তাহলে নতুন করে আরেকটি ভুলের প্রশ্ন উঠবে নিশ্চত করে বলা যায়।
সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, যা কিছুই হোক- যেন উন্মুক্ত খোলা আলোচনা এবং সম্ভাব্যতা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফের যেন কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে শির্ক্ষীদের ঠেলে দেওয়া না হয়।
লেখক: শাহনূর শাহীন
যুগ্ম সম্পাদক, পাবলিক ভয়েস। শিক্ষার্থী তিতুমীর কলেজ।

