
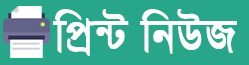
রিভিউ লেখক- আবদুল্লাহ আল মাসউদ
বিশ্বাসের বহুবচন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, অনেক সমালোচনা হয়েছে। বইটা তাই পড়ার তালিকায় ছিলো। গতো রাতে বইটা হাতে নিলাম। লেখকের লেখার জাদু ভালোই বিমোহিত করলো। তরতর করে এগিয়ে গেলো বহুবচনের পাঠ। একটানা শেষ করেছি বলা যায় বইটি। এবার মূল্যায়নের পালা।
বইয়ের শেষে পাঠকের পাতা রাখা ছিলো। সেটার সদ্ব্যবহার করতে কার্পণ্য করি নি। যখন যেটা আলাদা করে টুকে রাখার প্রয়োজন মনে হয়েছে, টুকে রেখেছি। বইটা পড়েছি সতর্কতার দৃষ্টিতে। লেখকের চিন্তার সূতোটা আবিষ্কারের প্রয়াসে ছিলাম পুরোটা সময়। তিনি কোন দিক থেকে কোন দিকে বাঁক নিচ্ছেন, পাঠককে কখন কোন সীমায় নিয়ে যাচ্ছেন সেসবও খেয়ালে রাখার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য।
আরও পড়ুন- আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. (গ্রন্থ পর্যালোচনা)
বিস্তারিত বয়ানে যাবার আগে সংক্ষেপে বইটার চিত্র তুলে ধরছি:
শুরুতেই ভূমিকামূলক কিছু কথাবার্তা এনে লেখক চলে যান সাক্ষাতকারপর্বে। সেখানে একেএকে হাজির করেন হেফাজতের কেন্দ্রিয় নেতৃবৃন্দকে। তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন অনুসন্ধিৎসু সূরে। মাঝেমাঝে একটু এদিক-ওদিকের আলাপ নিয়ে আসেন যাতে পাঠকের বিরক্তিবোধ জন্ম না নেয়। কুল্লু জাদীদ লাযীয বলে কথা। তারপর শাপলার আহত-নিহতদের নিয়ে প্রতিবেদন টাইপ কিছু পরিসংখ্যান ও তাদের পরিচয়-অবস্থার বর্ণনা। শাপলার অধ্যায় শেষ হলেই শুরু হয় শাহবাগের অধ্যায়। আগের মতোই শাহবাগের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের সাক্ষাতকার ও এদিক-ওদিকের আলাপ-সালাপ দিয়ে বইটার ইতি টানা হয়। সংক্ষিপ্ত চিত্রের পর এবার মূল্যায়নের মাঠে প্রবেশ করি।
শুরুতেই বইয়ের নাম নিয়ে বলি। শাহবাগের জন্ম আগে, শাপলার জন্ম পরে। কিন্তু বইর প্রচ্ছদেই আছে- শাপলা থেকে শাহবাগ। অনেক পাঠকের মুখে শুনেছি, এ কেমন বিষয়! ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেল না? আগে তো শাহবাগ, তারপর শাপলা।
আসলে যারা এমন প্রশ্ন তুলেছেন তারা এর ভেতরটা ঘেটে দেখেন নি। যদি দেখতেন তাহলে এমন প্রশ্নের উৎপত্তি হতো না। লেখক শাহবাগ নিয়ে যতটা বিচলিত ছিলেন তারচেয়ে শতগুণ বেশি বিচলিত ছিলেন শাপলা নিয়ে। তিনি চেয়েছেন শাপলার রহস্য তুলে আনতে। শাপলার অজানা অধ্যায় আবিষ্কার করতে। শাপলা নিয়েই ছিলো তার মূল কৌতুহল। তাই শাপলার আলোচনা তিনি আগে করেছেন। শেষে এনেছেন শাহবাগের কথা। অনেকটাই শাপলার আলোচনার পরিপূরক হিসেবে। সেই ধারাবাহিকতায় বইটি হয়েছে শাপলা থেকে শাহবাগ। এখানে কার থেকে কার জন্ম সেটা নির্দেশ করা উদ্দেশ্য নয়।
হেফাজতের ১৩ দফা নিয়ে আমার কিছু প্রশ্ন ছিল। আন্দোলনের উত্থান ও মূল বিষয় ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকতার বিরোধিতা। তো সেখানে এতগুলো দফা যুক্ত করে আন্দোলনকে কেন ভিন্নদিকে টেনে নেবার সুযোগ করে দেওয়া হলো শত্রুদেরকে তা আমার বোধগম্য হয় নি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আন্দোলনের এক পর্যায়ে হেফাজত নাস্তিক বিরোধিতার চেয়েও তারা যে নারী বিদ্বেষী নয় সেটা প্রমাণ করতেই ব্যতিব্যস্ত ছিল বেশি। কারণ কোন কোন দফাকে লুফে নিয়ে শাহবাগী মিডিয়াগুলো ও বুদ্ধিজীবিরা ব্যাপক প্রচারণা চালায় যে, হেফাজত নারী বিদ্বেষী। তারা নারীদের অধিকার চায় না। সেসময় লিফলেট-বুকলেট ছাপিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বিলি করে প্রচুর সময়-শ্রম ব্যয় করতে হয়েছিলো। আন্দোলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার এমন সুযোগ তাদের আমরা না করে দিলেও পারতাম। দফাগুলো কোনটাই ফেলনা নয়, তবে কথা হলো সেগুলো কেন এই আন্দোলনের ভেতরেই যুক্ত করতে হবে? আর যুক্ত করার যুক্তি যদি এটাই হয় যে, সবগুলো ধারা ইসলাম সমর্থিত তবে তো যুক্ত করার মতো আরও বহু বিষয়ই রয়ে গেছে। সেগুলো বাদ দেবার কারণ কী?
এত এত দফা দেবার কারণ কী ছিল সেটা তখন ভেবে পাই নি। জিজ্ঞাসাটা ভেতরে ছিলো। লেখক রশীদ জামীল সেই উত্তরটা আমাদের জন্য হাজির করেছেন বহুবচনের ৯২ পৃষ্ঠায়। মাইনুদ্দিন রূহির যবান থেকে। উত্তরটা আমাকে প্রচণ্ড রকমের অবাক করেছে। আপনাকেও অবাক করবে আশা করি। চলুন দেখে আসি কী ছিল মেই উত্তর।
রুহির ভাষ্য মতে যেহেতু তখন ছিল ২০১৩ সাল সুতরাং সেদিকে মিল রেখেই ১৩ দফা লেখা হয়। প্রশ্ন হল, ১৩ দফার পেছনে এই যদি হয় যুক্তি তবে কি এই আন্দোলন ২০২৩ সালে হলে একই যুক্তিতে আমরা ২৩ দফা পেতাম না? ২০১৩ সালের সাথে তাল রেখে ১৩ দফা রাখা বড় হাস্যকর মনে হয়েছে। ১৩ দফার সবগুলোই ইসলাম সমর্থিত দাবি। কিন্তু যে পেক্ষাপটে হেফাজতের জন্ম তার সাথে এর সবগুলোর তেমন জোরালো সম্পর্ক ছিল না। হেফাজতের নীতিনির্ধারকরাও যে কেন বিষয়টিকে এভাবে নিয়ে নিলেন বোধগম্য হলো না। মাইনুদ্দিন রূহি রাতভর জেগে ২০১৩ সালের সাথে মিল রেখে ১৩ দফা লিখে পরদিন মিটিংয়ে উপস্থাপন করলেন আর তারাও সেটা অনুমোদন দিয়ে দিলেন। একটুও বিবেচনা করলেন না, যে বিষয়কে সামনে রেখে তারা আন্দোলনের ডাক দিচ্ছেন তার সাথে এর যোগসাজশ কতোটুকু!
লংমার্চের দিন চরমোনাই পীর সাহেব কে মঞ্চে উঠতে দেওয়া হয়নি। যদিও দেওয়া হয়েছিল জাতীয় পার্টি, বিএনপিসহ অন্যান্য আরো অনেক দলের নেতাদেরকে। কেন দেওয়া হয় নি, কী ছিল তার পেছনের কারণ সেসব বিষয়ে ভাসাভাসা কথা শুনলেও বিশ্বাসের বহুবচন এই বিষয়ে মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছে। এক পক্ষ থেকে না হয়ে দুই পক্ষ থেকেই বিষয়টি উপস্থাপন করায় ভালোই হয়েছে। মোটামুটি ব্যাপার গুলো সামনে চলে আসলো। দরকার ছিল এমন কিছুর।
তবে লেখক পুরো বই জুড়ে যেই বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কৌতূহল দেখিয়েছেন তা হলো, শাপলার জমায়েত কার নির্দেশে হয়েছে, কেন সেখানে অবস্থান করা হলো, কারা এই পরিকল্পনা করলো ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হল, হেফাজতের নেতাদের বক্তব্য এক্ষেত্রে একেক জনেরটা একেক রকম। মুফতি ফয়জুল্লাহর ভাষ্যমতে শাপলা অবস্থানের বিষয়ে বাদ মাগরিব সিদ্ধান্ত হয়, মাঈনুদ্দীন রুহী বলেন দুই তিন দিন আগেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়, আল্লামা বাবুনগরীর ভাষ্যমতে ৫মে দুপুরে শাপলাতে জমায়েতের সিদ্ধান্ত হয়। এক বিষয়ে এমন পরস্পরবিরোধী মন্তব্য দেখে মন্তব্য করার মানসিকতা আর থাকে না।
১৬৫ পৃষ্ঠা থেকে ২০৫ পৃষ্ঠা আহতদের বর্ণনা, ২১৩ থেকে শহীদদের পরিচয় ও বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। আমি পৃষ্ঠাগুলো স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গিয়েছি। কারণ প্রথম জনেরটা পড়েই দেখলাম চোখের কোনায় নোনা পানি জমা হচ্ছে। এখন আর কানতে মনে চায় না। চোখের পানি ঝরাতে মন চায় না। আমার হৃদয় এখনো এতটা কঠোর হতে পারেনি যে, এমন হৃদয়-বিক্ষত ঘটনাগুলোকে হজম করতে পারে। তাই শুধু নামগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গিয়েছি। বিস্তারিত বিবরণ ঢুকতে পারিনি নিজের এই অপারগতার কারণে।
বইটি নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন কেন করেছেন এই বিষয়টি আমার কাছে এখনো পুরোপুরি সুস্পষ্ট নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে এমন একটা কিছুর লেখা দরকার ছিল। বইটির সব উপস্থাপন পুরোপুরি ঠিক সেটা আমি বলছি না। তবে লেখক যেভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলেছেন, হেফাজত নেতাদেরকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছেন এমনটা করার দরকার ছিল। তিনি প্রশ্নগুলো তুলেছেন, কোনটার উত্তর পাওয়া গেছে কোনটার উত্তর পাওয়া যায় নি। কোনটার উত্তর একেকজনেরটা একেক রকম হয়েছে। এভাবেই তো তথ্যানুসন্ধান এগিয়ে যায় সত্যের দিকে। লেখক সেই সত্যকে খুঁজে পেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন বলেই মনে হলো।
হেফাজত আন্দোলন নিয়ে লেখক পুরোপুরি মূল্যায়ন তুলে ধরতে পারেন নি- এমনটাই বলবো আমি। অবশ্য সেটা তার বইয়ের বিষয়ের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যশীল সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। তবে তিনি কেবল প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং আপত্তির পর আপত্তি তুলে ক্ষ্যান্ত হয়েছেন। সরাসরি কাউকে অভিযুক্ত করেন নি, আবার সন্দেহের তীর ছোঁড়া থেকে কাউকে রেহাই-ও দেন নি। পাঠকের ভেতর হেফাজত নেতৃবৃন্দের বিষয়ে সন্দেহের বীজ বপন করেই তিনি কেটে পড়েছেন। পাঠককে ছেড়ে দিয়েছেন নিজেদের মতো করে বিষয়টা বুঝে নিতে। অবশ্য এক্ষেত্রে সাক্ষাতকারদাতারাও লুকোচুরি করেছেন। তারা সরাসরি কিছু বলা থেকে যথাসাধ্য এড়িয়ে গিয়ে কৌশলী উত্তর দিয়েছেন। আর যারা মনের ডালি খুলে ভেতরের সব কথা বলেছেন তারা আবার তা লেখা যাবে না বলে লেখকের কলমে শেকল পরিয়েছেন। লেখকে তাই কতোটুকু দোষ দিবো ভাবছি!
তবে কয়েকটা বিষয়ে লেখককে অভিযুক্ত করাই যায়। তা হলো, তিনি হেফাজতের নেতাদের কেবল প্রশ্নবিদ্ধই করেছেন, কিন্তু হেফাজতের যে বিশাল অবদান আছে, যে বিশাল ত্যাগ ও কুরবানী আছে সেটা তেমন উঠে আসে নি তার কলমে। অথচ উঠে আসার দরকার ছিল।
শাপলা শব্দটা আমাদের আবেগের জায়গা। সেই শাপলাকে নিয়ে যখন লেখক ‘শাপলাবাজি’র মতো শব্দ ব্যবহার করেন তখন কেমন যেন তা সুঁই হয়ে খোঁচা দেয় মনের ভেতর। যদি ভেতরে কেউ ঘাপলা মেরে মুনাফিকি করেও থাকে তবে এর কারণে সেদিন শাপলাচত্ত্বরের হাজার হাজার মুমিনের তো কোন দোষ ছিল না। কিন্তু ‘শাপলাবাজি’ শব্দটা কেমন যেন পুরো শাপলার জনতাকে ও শাপলার সেই আন্দোলনকে হেয় করে তোলে। সেদিনের শাপলায় সশরীরে উপস্থিত আমি তাই সহজে শব্দটি মেনে নিতে পারি নি।
আরেকটা বিষয় হল, পুরা বইতে লেখক এই রক্তাক্ত ঘটনার জন্য হেফাজত নেতাদেরকে দায়ী করার চেষ্টা করেছেন। সরকারেরও যে বিশাল বড় দায় আছে এখানে সেটা তিনি অতটা বলেন নি বা বলতে পারেন নি। এক জায়গায় সামান্য টাচ দিয়েছেন যে সরকারেরও দায় আছে ব্যাস এতটুকুতেই খালাস। অথচ এটা আরও বড় করে তুলে ধরার দরকার ছিল। এমন সামান্য টাচ দিয়ে দায়টা যে কতো বেশি তার সামান্য অংশও ফুটে উঠে না। যদি সে কাজটি তিনি করতে পারতেন তবে বইটার সৌন্দর্য আরো বেশি বৃদ্ধি পেত। লেখককেও আমরা আরও বেশি সাধুবাদ জানাতে পারতাম, যা এখন পারছি না।
একটা বিষয় আমার এখনো বোধগম্য হয় নি। শাপলার আহত-নিহত ব্যক্তিদের তালিকা আজও আমরা জানতে পারি নি। জুনায়েদ বাবুনগরী বলেছেন তালিকা হয় নি। কিন্তু মাঈনুদ্দীন রুহী বলেছেন তালিকা হয়েছে। তার ভাষ্যমতে ‘এই তথ্যটা না বলার জন্য হুজুরের হাতে হাত দিয়ে আমাদের একটা ওয়াদা হয়েছে।’ আমার বোধগম্য হয় না, এই তথ্যটা গোপন রাখার এমন কী কারণ আছে। এটা কী এমন কোন বিষয়, যার জন্য হুজুরের হাতে হাত রেখে ওয়াদা করতে হবে যে এটা প্রকাশ করা যাবে না? সেদিন যারা শহীদ হয়েছেন তারা কি শহীদ হয়ে খুব বড় পাপ করেছেন যে তাদের নাম প্রকাশ পেলে এটা বড় লজ্জার কারণ হবে? নাকি শহীদ পরিবারের উপর হামলা-মামলা ও হয়রানির আশঙ্কায় এটি প্রকাশ করা হয়নি আল্লাহই ভালো জানেন। তবে কোনোদিন তালিকাটা তারা প্রকাশ করবেন আমরা সেই আশায় প্রহর গুণি।
সবশেষে আমি লেখককে সাধুবাদ জানাই। তিনি অনেক খাটাখাটনি করে বইটা রচনা করেছেন। বহু জনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন। যেই প্রশ্নগুলো আমার এবং আমাদের মন-মননে প্রতিনিয়ত ঘুরঘুর করে, যার উত্তর আমরা খুঁজে পাই নাই এখনও সেগুলো তিনি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। কতটুকু সফল হয়েছেন সেটা ভবিষ্যতই বলে দিবে। তবে তিনি যে চেষ্টা করেছেন সেটা তো বলতেই হবে।
বইয়ের প্রচ্ছদ চলনসই। তবে বাঁধাই আরো ভালো হওয়া দরকার। পাঠকদের কাছে আহ্বান থাকবে বিশ্বাসের বহুবচন পড়ে দেখতে পারেন। আপনারও অনেক অজানা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। নানা বিষয়ের দেখা পাবেন এতে। কোন কোন বিষয়ে লেখক এর সাথে সহমত না হতে পারলেও লেখক যে যৌক্তিক প্রশ্নগুলো ছুড়ে দিয়েছেন সেগুলো অন্তত জানতে পারবেন। সেই সাথে জানতে পারবেন আরো আরো অনেক কিছু, যা জানা আমাদের দরকার ছিল। এখনো, তখনও, সামনেও।
নাম : বিশ্বাসের বহুবচন
লেখক : রশীদ জামীল
প্রকাশনী : কালান্তর প্রকাশনী
মুদ্রিত মূল্য : ৩৪০
পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩৬৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮


